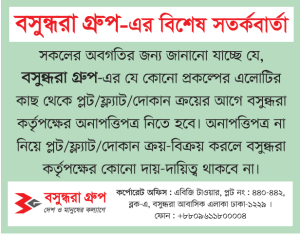বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ’
বিশেষ নিবন্ধ: বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ
আজ বুধবার- পয়লা বৈশাখ, ১৩৭৭ সাল। (লেখাটি ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ উপলৰে লিখিত) অন্য কথায় আজ বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন। দিনটিকে আমরা সচরাচর ‘নববর্ষ’ নামে চিহ্নিত করে থাকি। কারণ, ‘নববর্ষ’ আমাদের কাছে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের রূপ ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হবে।
পৃথিবীর সর্বত্র ‘নববর্ষ’ একটা ‘ট্রেডিশন’,- একটা ঐতিহ্য। এটি আবার এমন এক ‘ঐতিহ্য’, যার বয়সের কোন গাছপাথর নেই। গোড়ায় কোন সুনির্দিষ্ট বছরের সাথেও এর কোন যোগ ছিল ব’লে প্রমাণ পাওয়া যায় না; অথচ যে-কোন বছরের প্রথম দিনটি ‘নববর্ষ’ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এর মানে এ নয় যে, দিনটিই নতুন বছর। বরং, এর মানে হচ্ছে- নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য উৎসবের প্রথম দিন। প্রকৃতপক্ষে, ‘নববর্ষ’ একটা নির্দিষ্ট উৎসবের দিন।
আবার, পৃথিবীর সব নতুন বছরও এক সময়ে আরম্ভ হয় না। এতৎসত্ত্বেও ‘নববর্ষের’ নামের সাথে কতকগুলো ব্যষ্টিগত, আর কতকগুলো সমষ্টিগত অনুষ্ঠান চিরকাল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এ গুলোর কোন কোনটি ধর্মের রঙে রঙিন, কোন কোনটি মর্মের রঙে রঙিন। এবং কোন কোনটি ধর্ম ও মর্ম উভয় রঙে রঙিন। এ গুলোতে রঙের ছোপ কখন কিভাবে লাগল, তার আঁচ পাওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। তার জন্য মানব সভ্যতার ইতিহাসই যথেষ্ট বলে গণ্য হওয়া উচিত।
যতগুলো ‘অব্দ’ বা বৎসর পৃথিবীময় চালু ছিল বা আজও চালু আছে, তার সবগুলোই নির্দিষ্ট কালিক সীমারেখায় চিহ্নিত। অথচ, ‘নববর্ষের’ অনুষ্ঠানগুলোর অনেকটিকে কালিক সীমারেখায় চিহ্নিত করা যায় না। এ-গুলো যেন কালাতীত। তা হলে বুঝতে হয়, পৃথিবীতে পরিচিত বছরগুলোর আগে থেকেই এ-অনুষ্ঠানগুলো প্রতিপালিত হত এবং বছর গোনা শুরু হয়েছে এমন কতকগুলো অজ্ঞাতকুলশীল অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই। এ বিষয়ে আমরা যথাস’ানে বিশেষ আলোকপাত করবার চেষ্টা পাব।
‘নববর্ষে’ আমরা অতীত বৎসরের তিরোধান এবং সমাগত বৎসরের আবির্ভাবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে যাই। যে বছর প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিল, একদিকে তার সুখ-দুঃখের বহু স্মৃতিমাখা চিত্র বিলীয়মান এবং অন্যদিকে যে বছর প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল তার ভাবী, অথচ অনিন্ডিত সম্ভাবনা সুনিন্ডিতরূপে বিদ্যমান। মানুষের মনোরাজ্যের এই অবস’াটি অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।
প্রকৃতির রাজ্যে এক ঋতুর আগমনে যে নতুন পরিসি’তির উদ্ভব ঘটে, তা প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠে। এ-দেশের নয়, পৃথিবীর সব দেশের পশু-পক্ষীও প্রকৃতির পরিবর্তিত প্রভাব থেকে রেহাই পায় না। মানুষগুলোর শরীর ও মনে ছোঁয়া লাগে। আর, তারা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকে। এ -অনুষ্ঠানগুলোর ঢং আর রং সর্বত্র এক নয়। যুগে-যুগে দেশে দেশে মানুষের ধ্যান-ধারণা অনুসারে এ-গুলো ভোল পালটিয়েছে বটে, তবে এ-ভোলের আড়ালে তার যে আসল রূপ, তা বের করে নেওয়া এমন কোন শক্ত কাজ নয়। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা থাকলেই তা সহজে বেরিয়ে পড়ে। সঙসাজা, রংমাখা-মানুষ যেমন সঙ্ ও রঙের মধ্যে হারিয়ে যায় না, ভোল্-ফেরানো অনুষ্ঠানগুলোও তেমন ভোলের মধ্যে হারিয়ে যায় না।
দুই
‘পয়লা বৈশাখ’ বা ‘বাংলা নববর্ষের’ রূপ তার আচরিত অনুষ্ঠানগুলোতেই ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর যে-কোন জাতীয় উৎসবের রূপ তার প্রতিপালিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ‘বাংলা নববর্ষের’ জন্য এ কোন বিশিষ্ট ব্যবস’া নয়। ‘পয়লা বৈশাখ’ (অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনের তথা সারা বৈশাখ মাসের প্রতীকরূপী এই দিনে) বাঙালীর স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তচাঞ্চল্যের বহুমুখী অভিব্যক্তিই বড়-ছোট নানা অনুষ্ঠানে রূপ গ্রহণ ক’রে থাকে। তাই ‘পয়লা বৈশাখ’ বা ‘বাংলা নববর্ষকে’ বুঝতে হলে, এই দিনে প্রতিপালিত অনুষ্ঠানগুলোর একটা মোটামুটি হিসাব নিকাশ করে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হবে। এ অনুষ্ঠানগুলোকে মোট দু’ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- সার্বজনীন অনুষ্ঠান ও স’ানীয় অনুষ্ঠান।
(ক) ‘বাংলা নববর্ষের’ (অর্থাৎ ‘পয়লা বৈশাখের’) যে সমস্ত ‘স’ান’ ও পাত্র সাপেক্ষ নয়, সে-গুলোকে ‘সার্বজনীন অনুষ্ঠান’ নামে চিহ্নিত করা যায়। এ সমস্ত অনুষ্ঠান বাংলায় কোন নির্দিষ্ট স’ানে সীমাবদ্ধ নয়; শুধু হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ এ-গুলো পালন করে না। এ-গুলো এখনও সম্পূর্ণ না হলেও বেশ ব্যাপকভিত্তিক অনুষ্ঠান। এককালে এ-গুলো যে সার্বজনীন ও সর্বব্যাপক ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
‘পয়লা বৈশাখে’ বাংলার জনসমষ্টি অতীতের সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুনের আহবানে সাড়া দিয়ে ওঠে। তারা জানে, এ-নতুন অনিন্ডিতের সুনিন্ডিত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। তাই মন সাড়া দেয়, চঞ্চল হয়, নতুনকে গ্রহণ করার প্রস’তি নেয়। তারা সে-দিন প্রাত্যহিক কাজকাম ছেড়ে দিয়ে, ঘরবাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে, আটপৌরে জামা কাপড় ছেড়ে, ধোপদোরস্ত্ পোশাক-পরিচ্ছদ পরে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করে পানাহারে মেতে যায়; বটের তলায় জড় হয়ে গান গায়, হাতে তালি বাজায়, মুখে বাঁশী ফুঁকে, মাঠে-বাটে খেলায় বসে পড়ে, তড়াক-পুকুরে সাঁতার কাটে, ডুব দেয় ও নদ-নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সব কিছু মিলে দেশটা যেন হয়ে উঠে উৎসবমুখর। আর, এ-উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ হল কাঁচা আমের ‘ভর্তা’ ও শুঁটি আমের রস আস্বাদন। এ-সময়েই গাছে আম পুষ্ট হতে থাকে।
চৈত্রের শেষ ও বৈশাখের প্রথম থেকেই গ্রীষ্মের দাবদাহ শুরু হয়। এ-সময় আকাশ থেকে আগুন ঝরে; পশুপক্ষী গাছের ছায়ায় ঝিমুতে থাকে; মানুষের হাতে-হাতে তালের পাখা শোভা পায়; বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষগুলো ডাবের জলে তৃষ্ণা মেটায়; ডাবের শাঁসে অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে; দেশ জুড়ে চাতক ‘দে জল’ ‘দে জল’ বলে চেঁচাতে থাকে; আর উত্তর-বঙ্গের পাড়ায়-পাড়ায় সাঁঝের বেলা ‘আল্লা মেঘ দে, পানি দে’ বলে যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা সমস্বরে হাহাকার তোলে। মেঘের কাছ থেকে জল ভিক্ষা করাও ‘বাংলা নববর্ষের’ আর একটা সার্বজনীন অনুষ্ঠান।
বাংলা চিরদিনই কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্পের ছোঁয়াচ লাগলেও, এ-দেশ এখনও শিল্পায়িত হতে অনেক দেরি। আবার, এর কৃষি এখনও সেচনির্ভর নয়; বরং তার প্রায় সবটিই বৃষ্টিনির্ভর। বৃষ্টির জন্য চাই মেঘ। মেঘ না হলে বৃষ্টি হয় না; বৃষ্টি না হলে মাঠে লাঙল দেওয়া যায় না; লাঙল দেওয়া না গেলে মাঠে শস্য বোনাও একরূপ অসম্ভব। চাষবাসের সব কাজ বৈশাখ মাস থেকেই শুরু করতে হয়। এই রেওয়াজ এত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী যে, আজও চাষীদের মধ্যে অনেকেই, চৈত্রি-মাসে বৃষ্টি হলেও, বৈশাখ মাসের আগে মাঠে চাষ দেয় না। তারা মনে করে, চৈত্রি মাসে শস্য বুনলে, সে-শস্য ফলে না। এ লৌকিক ধারণার সত্যতা যাচাই সম্ভব হয়নি।
‘বাংলা নববর্ষের’ সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে ‘বার্ষিক মেলার’ আয়োজনও একটি। বাংলা দেশের নানা স’ানে সারা বৈশাখ মাস ধরে বিশেষ করে পয়লা বৈশাখে, বড়-ছোট নানা ‘মেলা’ বসে। স’ানীয় লোকেরাই এ-সব মেলার আয়োজন করে থাকে। মেলাগুলোর স’ায়িত্বকাল এক থেকে সাত দিন। উত্তর-বঙ্গের দিনাজপুর জেলার নেকমর্দানে এখনও পয়লা বৈশাখে যে ‘মেলা’ বসে, তা হচ্ছে উত্তর-বঙ্গের সব চাইতে বড় মেলা। এ-‘মেলা’ এক সপ্তাহকাল স’ায়ী হয়। এতে উত্তর-বঙ্গের হেন বস’ নেই, যা পাওয়া যায় না। জনসাধারণের আনন্দ দানের উপযোগী আয়োজনও এ-‘মেলায়’ কম থাকে না। তন্মধ্যে নাচ, গান, নাগরদোলা প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
‘বাংলা নববর্ষের’ ‘পুণ্যাহ’ নামক আরও একটি অনুষ্ঠানও সার্বজনীন। ‘পুণ্যাহ’ শব্দের মৌলিক অর্থ ‘পুণ্য কাজ অনুষ্ঠানের পক্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন।’ কিন’, বাংলায় এর অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে ‘জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে নতুন বছরের খাজনা আদায় করার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানসূচক দিন।’ এই সে-দিন (১৯২০) পর্যন্ত জমিদার ও বড় বড় তালুকদারের কাছারিতে ‘পুণ্যাহ’ অনুষ্ঠিত হত। যদিও অধিকাংশ ‘পুণ্যাহ’ পয়লা বৈশাখে উদযাপিত হত, বেশ কিছুসংখ্যক ‘পুণ্যাহ’ সারা মাস ধরে পুর্বনির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হত। সে-দিন অধিকাংশ প্রজা ভাল কাপড়-চোপড় পরে জমিদার-তালুকদার বাড়িতে খাজনা দিতে আসতেন। প্রজারা নতুন বছরের অথবা অতীত বছরের খাজনা আংশিক বা পুরোপুরি আদায় করতেন। কোথাও কোথাও মিষ্টিমুখ করাতেন। ঐ দিন জমিদার প্রজার সম্বন্ধের দূরত্ব খুব কমে আসত। তাঁরা পরস্পর মিলিত হতেন, পরস্পরের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন, এমন কি পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। এখন আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।
(খ) বাংলা ‘নববর্ষের’ স’ানীয় অনুষ্ঠান বহু। এ-গুলোর পূর্ণ অনুসন্ধানের জন্য দীর্ঘ ও বহু পরিশ্রমসাপেক্ষ গবেষণার প্রয়োজন। সে কাজে নতুন করে প্রবৃত্ত হওয়ার শারীরিক সামর্থ্য ও আবশ্যক সময় না থাকায় আমরা নিম্নে কয়েকটি সুপরিজ্ঞাত অনুষ্ঠানের উল্লেখ করছি। বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো এখন দেশের সর্বত্র প্রচলিত নেই। তবে, দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। এ হিসেবেই এ গুলো স’ানীয়।
‘হালখাতা’-র অনুষ্ঠান ‘পয়লা বৈশাাখের’ আর একটি সার্বজনীন আচরণীয় রীতি।
আমাদের দেশের সব শ্রেণীর ব্যবসায়ীর, অর্থাৎ দেশীয় ধরনের যাঁরা ব্যবসায়ের হিসাব রাখেন তাঁদের মধ্যেই এই অনুষ্ঠানটির প্রচলন এখনও বর্তমান। তবে, অর্থনৈতিক কারণে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাবে ‘পয়লা বৈশাখের’ এই অনুষ্ঠানটির জাঁকজমক এখন বেশ কিছুটা কমে গেছে। কিন’, ‘হালখাতা’ এখনও যথারীতি খোলা হয়। এখনও ব্যবসায়ীদের বিপণিগুলো ‘পয়লা বৈশাখে’ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে পতাকা, লতা-পাতা প্রভৃতি দিয়ে সাজানো হয়। এখনও এই দিনে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলোতে বেচাকেনার চেয়ে আলাপ-আলোচনা ও সামাজিকতার পরিচয় পাওয়া যায় বেশী।
‘হালখাতা’ নতুন বাংলা বছরের হিসাব পাকাপাকিভাবে টুকে রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের নতুন খাতা খোলার এক আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ। এতে তাঁদের কাজ-কারবারের লেনদেন, বাকী-বকেয়া, উসুল-আদায়- সব কিছুর হিসাব-নিকাশ লিখে রাখার ব্যবস’া করা হয়। নানা কাজ কারবারে তাঁদের সাথে যাঁরা সারা বছর জড়িত থাকেন অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের নিয়মিত গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভার্থী, তাঁদেরকে পত্রযোগে অথবা লোক মারফত দাওত দিয়ে দোকানে একত্র করে সাধ্যমতো জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। এ-আপ্যায়ন একান্ত সৌজন্যমূলক হলেও, এ সুযোগে অনেকে তাঁদের বাকী-বকেয়াও শোধ করে দেন, যেন ‘হালখাতায়’ বাকীর ঘরে তাঁদের নাম স’ান না পায়। নেহাত অসমর্থ না হলে কেউ বাকীর ঘরে নাম তুলতে চান না। তাঁদের কাছে এটা একটা অপমানজনক ব্যাপার। এ-দিক থেকে লক্ষ্য করলে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যে, ‘হালখাতা’-অনুষ্ঠান ‘পুণ্যাহ’-অনুষ্ঠানেরই ও-পিঠ। উভয় অনুষ্ঠানের সামাজিকতা, লৌকিকতা, সমপ্রীতি ও সৌজন্যের দিকও লক্ষণীয়।
(১) ‘আমানি’ : ইহা বাংলা ‘নববর্ষের’ স’ানীয় অনুষ্ঠান হলেও, এক সময়ে দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলে মনে করার কারণ আছে। তবে, অনুষ্ঠানটি এখন যেমন, পূর্বেও তেমন সমারোহহীন ছিল। ১৯৭০ ইংরেজীর ২রা মে তারিখের ‘পাকিস্তান অবজার্ভার’ নামক ঢাকার ইংরেজী দৈনিকে ফিল্ম-পরিচালক ও প্রযোজক খান আতাউর রহমান সাহেবের ‘জয় বাংলা’ শীর্ষক যে দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এ-প্রদেশের ‘নববর্ষে’ অনুষ্ঠিত এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এর কোন নাম দেননি। তবে, তিনি বলেছেন, এ-প্রদেশের অতি ধার্মিক পরিবারেও তিনি এ-অনুষ্ঠানটি ‘পয়লা বৈশাখে’ প্রতিপালিত হতে দেখেছেন। বৈশাখ মাসে প্রাতে এক থাল ‘পান্তা’ খেয়ে মাঠে লাঙল দিতে বার হতে আমিও বাংলার কয়েক জেলার চাষীকে দেখেছি। তাই বলছিলাম হয়তো অনুষ্ঠানটি এক সময় দেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। জনাব খান আতাউর রহমান সাহেব প্রদত্ত বর্ণনাটি নিম্নে দেওয়া গেল :
চৈত্রি-মাসের শেষ দিনের (অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির শেষ দিন গত রাত্রে) সন্ধ্যায় গৃহিণীরা এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ব (আম) চাউল ছেড়ে দিয়ে সারাটি রাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটা কচি আমের ডাল বসিয়ে রাখেন। ‘পয়লা বৈশাখের’ ভোর বেলায় সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠে তাঁরা (গৃহিণীরা) ভিজা চাল গৃহের সকলকে খেতে দেন। ঘরের সবাই মিলে অথবা একে একে তা খেতে থাকে; আর হাঁড়িতে ডোবা আমের শাখা দিয়ে গৃহিণীরা সকলের গায়ে পানি ছিটাতে থাকেন। তাঁদের ধারণা,-এতে করে গৃহে নতুন বছরের শান্তি নেমে আসবে।
এখনও চট্টগ্রাম জেলার গ্রাম-দেশে বৈশাখ মাসের সকাল বেলায় এক মুঠো চাল ও এক ‘কত্তি’ (নল বিশিষ্ট মাটির পানপাত্র) ঠান্ডা পানি খেয়ে অনেক চাষী মাঠে লাঙল দিতে যায়। তারা বলে, এতে শরীর সারা বেলা ঠান্ডা থাকে। মনে হয় এও ‘আমানির’ আর এক সংস্করণ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ‘আমানি’ শব্দটি ‘আমপানীয়’ অথবা অমৱ পানীয়- এই দুই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করে থাকবে। শব্দ দুইটির বিবর্তনের ধারা এইরূপ :
আমপানীয়>আমআনিঅ>আমআনি> আমানি; অর্থাৎ
অসিদ্ধ (আম) চাউল জাত জল।
আম্লপানীয়> অম্মআনিঅ> আমআনি> আমানি; অর্থাৎ
সিদ্ধ চাউলজাত টক পানীয়; পান্তাভাতের পানি; কাঁজি।
এখানে আমাদের ‘নববর্ষের’ ‘আমানির’ অর্থে প্রথম শব্দটি (আমপানীয়) প্রযোজ্য। এটা আদিমতম রীতির পরিচায়ক। দ্বিতীয় শব্দটি সভ্যতার পরবর্তী স্তরের। এই স্তরে মানুষ পাক করতে ও তাকে সঞ্চয় করে রেখে বাসী করে খেতে শিখেছে। সভ্যতার এ স্তরে আমাদের দেশের মানুষ ‘আমানি’ বা ‘কাঁজি’ খেয়েও ‘নববর্ষের’ উৎসবে যোগ দেওয়ার প্রস’তি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং শব্দটির দুই ব্যুৎপত্তিই গ্রাহ্য।
(২) ‘গম্ভীরা’ : এও একটি স’ানীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান মুখ্যতঃ ভারতের মালদহ জেলায় এবং গৌণতঃ মালদহের যে অংশ (নবাবগঞ্জ ও ভোলারহাট থানাদ্বয়) রাজশাহীর সাথে বর্তমানে যুক্ত আছে, তাতে চালু রয়েছে। ফলে, এখন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার শহর ও মফস্বল এলাকায় প্রতি বৎসর সারা বৈশাখ মাস জুড়ে ঘটা করে না হলেও নীরবে গম্ভীরা অনুষ্ঠিত হয়।
‘গম্ভীরা’ লোক-গীতি ও লোক-নৃত্যের অনুষ্ঠান। ‘পয়লা বৈশাখ’ থেকে শুরু করে সারা মাস রাজশাহীর নানা স’ানে গম্ভীরার আসর আয়োজিত হয়। সাধারণতঃ রাত্রি নটা থেকে রাত্রি বারটা একটা পর্যন্ত এ আসর চলতে থাকে। স’ানীয় লোক-কবিরাই ‘গম্ভীরা’-গানের রচয়িতা ও মূল গায়েন। মূল গায়েনই কয়েকজন দোহার নিয়ে দল বাঁধেন। তিনি বিগত বছরের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের ঘটনা অবলম্বন করে গান বাঁধেন ও গাহেন, আর দোহারেরা অঙ্গভঙ্গি সহকারে নেচে ও গেয়ে গানের কথার রূপ দেন। দর্শকেরা (নিমন্ত্রিতের চেয়ে রবাহুতের সংখ্যাই বেশি) তা শুনে ও দেখে আনন্দে আত্মহারা হন। গানের ভিতর দিয়ে সমাজের পদস’ লোকদের অতীত বছরের কাজের সমালোচনা করাই ‘গম্ভীরা’ গানগুলোর মূল উদ্দেশ্য। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি গানের দুটো কলি স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করছি। ১৯৪৪ ইংরেজীর ‘পয়লা বৈশাখ’। মালদহ পৌরসভার এক ভাইসচেয়ারম্যানের উপর জনহিতার্থে কিছু চাঁদা উঠাবার ভার পড়ে। তাঁর তিন স্ত্রী এবং তিনি একজন উকিল। সন্ধ্যার সময় তিনি গোপনে একাকী ছোটলোকদের সাথে আমবাগানে ‘পচাই’ খেতেও যেতেন। চাঁদা উঠানোর দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যর্থ হন। তাঁকে সমালোচনা করে পয়লা বৈশাখে ‘গম্ভীরা’-য় গাওয়া হল :
‘বলনা ভোলা, করি কি উপায়,
আমার বাজে কাজে সময় নাই।
দিনের বেলায় নানান হালে,
কোর্ট কাচারি মুন্সীপালে,
কেটে যায়রে দিন আমার-
মরি হায় রে,…
পালতে তিনটি দুধের গাই,
করি কি উপাই।
সন্ধ্যা হলে ঘরে আসি
মুখে আমার রয়না হাসি,
মরি হায় রে,…
তাইতো আমি সাঁঝের বেলায়
আমবাগানে হাওয়া খাই।
আমার বাজে কাজে সময় নাই’।
বলাবাহুল্য, ভদ্রলোকটির উপসি’তিতেই আসরে এ-গান গাওয়া হচ্ছিল। আমি পাশে উপবিষ্ট। তিনি হাসছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এ বিদ্রুপ বাণ কার প্রতি ছোড়া হচ্ছে? তিনি হেসে উত্তর দিলেন, ‘বুঝলেন না? আমাকে।’ আমি ভাবতে লাগলাম, ‘এতো বড় মজার ব্যাপার!’ দেখলাম,- সমালোচনা যতই কুৎসিত ও কঠোর হোক, সমালোচক ও সমালোচিতের মধ্যে তা কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। অথচ, সমালোচিতেরা আগত বছরে নিজেদের শোধরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ-দিক থেকে ‘গম্ভীরা’ গান অত্যন্ত গণমুখী ও গণতান্ত্রিক।
(৩) বলীখেলা : এটির প্রচলন কেবল চট্টগ্রাম জেলায় সীমাবদ্ধ। ‘পয়লা বৈশাখ’ থেকে শুরু করে সারা মাস ধরে এ জেলার নানা স’ানে ভিন্ন ভিন্ন দিনে বলীখেলার আয়োজন করা হয়। মৌলভী সাহেবেরা এ-যাবৎ প্রাণপণ চেষ্টায় ধর্মের দোহাই দিয়েও ‘বলীখেলা’ বন্ধ করতে পারেননি। এ-অনুষ্ঠানে স’ানীয় ও দূর-দূরান্তের কুস্তিগীরেরা নেচে কুঁদে কুস্তি লড়ে শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। বিজয়ী কুস্তিগীরদেরকে কাপড় ও নগদ অর্থে পুরস্কৃত করা হয়। যদিও ‘পয়লা বৈশাখ’ এ-বলীখেলার জন্য প্রশস্ত দিন বলে সাধারণভাবে গণ্য করা হয়, তথাপি বৈশাখ মাসের যে-কোন দিনে এ-খেলা আয়োজিত হতে পারে। প্রত্যেক ‘বলীখেলার’ সাথে একটা সাময়িক মেলাও বসে থাকে। ঢোলের বাদ্য ও সানাইয়ের সুরই এ খেলার আনুষঙ্গিক সঙ্গীত। যাঁরা ‘বলীখেলার’ আয়োজন করেন, তাঁরাই এ-বাদ্যের আয়োজন করে থাকেন। কোন কোন খ্যতনামা কুস্তিগীরের দলও সঙ্গে নিজেদের বাদক-দল খেলার মাঠে নিয়ে আসেন।
চট্টগ্রামের ‘বলীখেলা’-গুলোর মধ্যে শহরের ‘আবদুল জবক্ষারের বলীখেলাই’ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এ ‘বলীখেলার’ জন্য কোন নির্দিষ্ট তারিখ নেই। আবদুল জবক্ষারও একজন খ্যাতনামা ‘বলী’ ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি তাঁর নামে ‘বলীখেলার’ আয়োজন করতেন; কিন’ কুস্তি লড়তেন না। এখন তিনি নেই কিন’ তার ‘বলীখেলা’ বৈশাখ মাসের কোন নির্দিষ্ট দিনে এখনও ফি-বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাতে বড় বড় সরকারী অফিসারেরাও দর্শকরূপে যোগ দিয়ে থাকেন। এ-বলীখেলায় শান্তিরক্ষার জন্য বহু পুলিশ নিয়োজিত হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম শহরের ‘লালদীঘি ময়দানেই’ এ-বলীখেলা আয়োজিত হয়ে থাকে।
(৪) গরুর দৌড় : ‘নববর্ষের’ স’ানীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে ‘গরুর দৌড়’ অন্যতম। এ-অনুষ্ঠানটি এখন একরূপ লোপ পেয়েছে। মাত্র বছর চল্লিশেক আগেও, ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামে-গ্রামে ‘পয়লা বৈশাখে’এ অনুষ্ঠান সমারোহসহকারে উদযাপিত হত। যে সমস্ত জায়গায় ‘গরুর দৌড়’ হত, তথায় ছোটখাট মেলাও বসত। এ-দিন সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহসে’রা তাদের হালের গরুর গায়ে রঙের ছোপ দিয়ে, গলায় কড়ির মালা পরিয়ে সাজাতেন এবং গরুগুলোকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেন। যাঁদের গরু এ প্রতিযোগিতায় জিতত, গৌরবে তাঁদের বুক ফুলে উঠত এবং তাঁরা আনন্দে ফেটে পড়তেন।
এর থেকে দেখা যাবে, ‘বাংলা নববর্ষ’ সচরাচর ‘পয়লা বৈশাখে’ প্রতিপালিত হলেও এটা সারা বৈশাখ মাসব্যাপী পালনীয় অনুষ্ঠান। এতে কোন ধর্মের প্রভাব নেই বলেই, বিশেষ কোন দিন বা দিনসমষ্টির প্রতি এর কোন বিশিষ্ট প্রবণতা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ‘গম্ভীরা’ যদি হিন্দুদের ‘শিবের গাজন’ হত, তাহলে এ অনুষ্ঠান নিন্ডয় চৈত্রসংক্রান্তিতে আরম্ভ ও শেষ হত। কারণ, চড়ক পূজা ও শিবের গাজন চৈত্রসংক্রান্তি ছাড়া অন্য সময় হতে পারে না, আবার, ‘আমানি’ খাওয়া কেবল ‘পয়লা বৈশাখের’ গার্হস’্য অনুষ্ঠান হলেও তার সাথে কোন বর্ষের কোন বিশিষ্ট অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপ যুক্ত হয়নি। ‘বলীখেলা’ ও বৈশাখ থেকে শুরু হয় ও সারা বৈশাখ মাস ধরেই চলে। ‘পুণ্যাহ’ও অনুরূপ অনুষ্ঠান ছিল। একমাত্র ‘হালখাতার’ অনুষ্ঠানটিই পয়লা বৈশাখ প্রতিপালিত হয়। কারণ, সেদিন যে নতুন খাতার মহরৎ হয় তা অন্য দিনে চলে না। ব্যাপারটি সাংবৎসরিক হিসাব রাখার বিষয় বলে, যাতে হিসাবে কোন গোল না বাঁধে, তার ব্যবস’া বাধ্য হয়েই নির্দিষ্ট দিনে রাখতে হয়। ‘মেলা’ও দেশ জুড়ে সারা বৈশাখ মাসেই বসে, যদিও ‘পয়লা বৈশাখে’ অনেক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ-কথা ঠিক যে, ‘পয়লা বৈশাখ’ একটা ঐতিহ্যময় উৎসবের দিন। মেলায় তার চরম অভিব্যক্তি ঘটে, এখানে এসে মানুষ মানুষের সাথে মিলিত হয়, ক্ষুদ্র মানুষ বৃহৎ হয়, সীমাবদ্ধ মানুষ সীমা ছাড়িয়ে যায়, সে নিজেকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে এবং অপরকে নিজের মধ্যে ঠাঁই দেয়। মানুষের মেলায় আনন্দ নির্মল ও নিঃস্বার্থপরতার আনন্দ। কেবল কলুষিত মানুষই মেলাকে কলুষিত করতে পারে। তার জন্য মেলা দায়ী নয় ঐ শ্রেণীর মানুষই দায়ী।
তিন
উৎসবরূপে ‘নববর্ষ’ উদযাপনের রেওয়াজ বাঙালীর একার নয়। পৃথিবীতে সুসভ্য, অর্ধসভ্য অথবা অসভ্য এমন কোন জাত নেই, যাঁরা ঘটা করে ‘নববর্ষ’ পালন করেন না। তাও যে একই সময়ে একই ধরনে উদযাপিত হয়, এমন নয়। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ‘নববর্ষ’ এখন জুলিয়ান পঞ্জিকার বহুল প্রচলনের ফলে একই তারিখে (প্রথম জানুয়ারিতে) প্রতিপালিত হলেও, আগে তা হত না। কারণ, একেবারে আদিতে আদিম মানুষ ‘নববর্ষ’ পালন করত সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে ঋতু পরিবর্তন দেখে। সুতরাং, আদিতে ‘নববর্ষ’ ছিল ‘আর্তব উৎসব’(ঝবধংড়হধষ ভবংঃরাধষ)।
পৃথিবীর সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ইতিহাসে উৎসবরূপে পালিত ‘নববর্ষের’ উদযাপনকালগুলো লক্ষ্য করলেই উপরোক্ত কথার তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হবে : প্রাচীন মিশরীয়, ফিনিশীয় ও ইরানীয়গণ ‘নববর্ষের’ উৎসব পালন করতেন শারদীয় বিষুব দিনে (অঁঃঁসহধষ ঊয়ঁরহড়ী) ২১শে সেপ্টেম্বরে; প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত) এ উৎসব পালন করতেন সূর্যের দক্ষিণ অয়নাস্ত দিনে (ডরহঃবৎ ঝড়ষংঃরপব) ২১শে ডিসেম্বর; প্রাচীন ইহুদীগণ এ উৎসব উদযাপন করতেন বাসন্ত বিষুব দিনে (ঠবৎহধষ ঊয়ঁরহড়ী) ২১শে মার্চে; ইংল্যান্ডের এ্যাঙ্গলো সেক্সনগণ এ উৎসব পালন করতেন সূর্যের দক্ষিণ-অয়নাস্ত দিনে (ডরহঃবৎ ঝড়ষংঃরপব) ২৫শে ডিসেম্বর; তিব্বত, শ্যাম (থাইল্যান্ড) ও ভিয়েৎনামে সৌরমাস-সমন্বিত চান্দ্রমাসের হিসাবে এ উৎসব প্রতিপালিত হত ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায়, মধ্যে অথবা শেষ ভাগে; প্রাচীন আরবগণ চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাস মহরমে আন্তর্গোত্রিক যুদ্ধ বিগ্রহ, বিবাদ বিসংবাদ বন্ধ করে উকাজের মেলায় যোগ দিয়ে খেলাধুলা ও পানাহারে মেতে ‘নববর্ষের’ উৎসব পালন করতেন। প্রাচীন ইরান ও প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যজাতির ‘নববর্ষ’ পালনের সময় ও পদ্ধতি প্রায় একরূপ ঝিল। এরা সৌরমাস সমন্বিত চান্দ্রমাসের হিসাবে ‘নববর্ষের’ উৎসব পালন করতেন। ইরানে ছয়দিন ধরে ‘নওরোজ’ এবং ভারতে তিন দিনব্যাপী ‘দোল’ উৎসব এই ‘নববর্ষ’ জ্ঞাপক উৎসব। ‘দোল’ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। ‘নওরোজ’-ও ফাল্গুন মাসের মধ্যেই উদযাপিত হয়।
‘নওরোজ’ ও ‘দোলের’ মতো পৃথিবীর নানা দেশে ‘নববর্ষের’ অনুষ্ঠানগুলোর বিশিষ্ট বিশিষ্ট নামও দেখা যায়; যেমন- তিব্বতীরা ‘নববর্ষের’ উৎসবকে ‘লোগ্সর’, শ্যামবাসীরা ‘ত্রাত’, ভিয়েৎনামীরা ‘তেত’, খ্রীস্টানেরা ‘খ্রিস্টমাস’ (নিউ ইয়ার), ইহুদীরা ‘রূশ হশানা’ এবং মুসলমানেরা ‘আশুরা’ (আশুরা মুসলমানদের নববর্ষ তথা হিজরী বছরের শুরুর কোন উৎসব নয়, বরং তা কারবালার মহা বিয়োগাত্বক ঘটনার শোকবহ দিন -সম্পাদক) নামে চিহ্নিত করে থাকে। বলাবাহুল্য, ‘আশুরা’ মহর্রম মাসের ১০ই তারিখে একটা (এবং কেহ কেহ তিনটা ৯, ১০ এবং ১১ই মহর্রমে) রোজা রেখে ব্রতরূপে উদযাপন করা হয়। এ-সবের প্রত্যেকটির সাথে বহু অনুষ্ঠান জড়িয়ে আছে এবং তার প্রায় সব কটিই ধর্মসম্পৃক্ত। এর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ‘নববর্ষ’ ও তার অনুষ্ঠান প্রাচীন- এত প্রাচীন যে, তখনও মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগেনি। পরে- বহু বহু পরে তার সাথে ধর্মবোধ ও আচারনিষ্ঠা যুক্ত হয়েছে।
একমাত্র মুসলমান ছাড়া, পৃথিবীর সভ্য-অসভ্য সমস্ত জাতি এই আনন্দময় পরিবেশে ‘নববর্ষ’ পালন করতেন এবং এখনও করেন। নাচ নেচে, গান গেয়ে, ভুরিভোজন করে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পানাহারে মেতে, আত্মীয়-পরিজনের সাথে মিলিত হয়ে, স’ানে স’ানে আড্ডা দিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে ‘নববর্ষের’ বাঞ্ছিত উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করা হত ও এখন পর্যন্ত হচ্ছে। কিন’ মুসলমানেরা ‘আশুরার’ রোজার পরে মাতম করে, বুক চাপড়িয়ে ‘গওয়ারা’ বানিয়ে কারবালার বিষাদান্তক ঘটনার অভিনয় করেন। (এটি শিয়া সমপ্রদায়ের একটি আচার, মুসলমানদের সার্বজনীন কোন আচার নয় -সম্পাদক)
খ্রীস্টাব্দ, হিজরী-অব্দ, শকাব্দ, বিক্রমাব্দ, বুদ্ধাব্দ অথবা বঙ্গাব্দ প্রভৃতি কোন নির্দিষ্ট বছরের সাথে ‘নববর্ষের’ কোন যোগ নেই, অর্থাৎ কোন প্রকারের বৎসর গণনার প্রারম্ভ থেকে কোন দেশের অথবা জাতির ‘নববর্ষ’ শুরু হয়নি। এ হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসা একটা বাৎসরিক উৎসব। কোন ধর্মের সাথেও ‘নববর্ষের’ কোন সম্পর্ক নেই। বিশিষ্ট বৎসরগুলো যেমন পরে এসে এতে যুক্ত হযেছে, বিশিষ্ট ধর্মও তেমন এতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। প্রকৃতপক্ষে, বয়সের তুলনায় ‘অব্দই’ বলুন, আর ‘ধর্মই’ বলুন, ‘নববর্ষের’ উৎসবের কাছে নেহাত সেদিনের খোকা; আধুনিক ‘নববর্ষ’ উৎসবের মধ্যেই আদিম ‘নববর্ষের’ উৎসব পরিবর্তিত রূপ নিয়ে লুকিয়ে আছে। তাই, তার প্রাচীন অনুষ্ঠানাদিকে আধুনিক অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে থেকেই খুঁজে বার করতে হবে। এখানেই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের স্মরণ নিতে হয়।
মানব-সভ্যতার যাযাবর অবস’ায় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চন্দ্রকলা (তিথি) ভিত্তিক ‘মাস’ ও ‘বৎসর’ গণনা প্রচলিত ছিল। কারণ, আদ্যন্তবিহীন কালের ‘মাস’ বা ‘বৎসর’ বিভাগ নির্ণয় করার জন্য চন্দ্রের তিথি বা কলা দেখে দিন মনে রাখা সরল আদিম মানুষের পক্ষে যত সহজ, সূর্যের উদয়াস্ত দেখে দিন মনে রাখা তত সোজা ছিল না। কেননা, ত্রিশ দিনের মধ্যে চাঁদ বাড়তে বাড়তে পূর্ণ হয় এবং ক্ষয় পেতে পেতে লোপ পায়। এটা মানুষের চোখের সামনেই ঘটত। তাই সে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের এক চাঁদের সি’তিকালকে অনন্ত সময়ের মধ্যে ফেলে মেপে নিয়ে ‘মাস’ নামে একটা ভাগ করে নিত। শীত, বর্ষা বা গ্রীষ্ম যে কাল থেকে চাঁদের কাঠিতে সময় মাপা শুরু হত, ঠিক বার চাঁদ পরে সে আবার সে সময়টিতে (শীত, বর্ষা বা গ্রীষ্মে) এসে উপসি’ত হত। তাই, বার মাসে হত তার ‘বছর’। এ চান্দ্র বছর যে ছোট, তখনও সে জ্ঞান তার হয়নি।
এ-জ্ঞান (অবশ্য সময় সম্বন্ধে) নিয়ে মানব-সভ্যতা যখন ‘কৃষিযুগে’ প্রবেশ করল, তখন দেখা দেখা গেল, এতে কৃষিকাজে ব্যাঘাত ঘটেছে। কেননা কৃষিকাজের জন্য বছরের সুনির্দিষ্ট সময় আবশ্যক হচ্ছে; শস্য বপনেরও নির্দিষ্ট সময় চাই, শস্য সংগ্রহেরও নির্দিষ্ট সময় চাই। অথচ, চান্দ্রমাসের হিসাবে তা ঠিক রাখতে পারা যাচ্ছে না। সময় ঠিক রাখতে গিয়ে তাকে প্রতি তিন বছরে এক চান্দ্র মাস বাড়িয়ে দিতে হচ্ছে। নইলে কৃষির উপযুক্ত শীত, বর্ষা ও গ্রীষ্মকাল পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তাকে বাধ্য হয়েই চান্দ্র সৌর বৎসরভিত্তিক বছর গণনা শুরু করতে হয়। কারণ, সৌর বৎসরের মাসগুলো ঠিক সময়েই আসে। এর দিন সংখ্যা ৩৬৫; কিন’ চান্দ্র বৎসরের দিন সংখ্যা ৩৫৪ দিন ৯ ঘন্টা।
অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, পৃথিবীর প্রাচীন-সভ্যতার অধিকারী প্রায় সমস্ত জাতিই চান্দ্র সৌর বৎসর অনুসরণ করতেন। প্রাচীন মিশরীয়, প্রাচীন বাবিলনীয়, প্রাচীন চৈনিক, প্রাচীন ইহুদী ও প্রাচীন ভারতীয় পঞ্জিকা চান্দ্র সৌর মাস হিসাবেই চলত। এখনও ভারতীয় হিন্দু পঞ্জিকায় যাবতীয় পূজা-পার্বণ চন্দ্রের তিথি অনুসারে সৌরমাসের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে সম্পাদিত হবার ব্যবস’া দেওয়া আছে। অথচ কৃষি ও বিবাহাদির বেলায় সৌর মাসের হিসাবেই ব্যবস’া দেওয়া থাকে। শুভাশুভ নির্ণয়ের ব্যাপার জ্যোতিষিক। মোটের উপর, বর্তমান ভারতীয় পঞ্জিকা অত্যন্ত জটিল (ঝড়ঢ়যরংঃরপধঃবফ)। ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনের ফলেই, এ সমস্ত জটিলতা সম্ভব হয়েছে। এর বিবেচনা এ-স’লে এই প্রসঙ্গে একরূপ অবাস্তব। মোটের উপর, ভারতীয় পঞ্জিকাও চান্দ্র সৌরধর্মী বলে কৃষি ভিত্তিক।
নতুন বছরের আগমন ও পুরনো বছরের অবসানসূচক অনুষ্ঠানাদিও রকমারি। যে-সমস্ত মানব-গোষ্ঠী এ-অনুষ্ঠানাদি পালন করে, তাদের সংখ্যাও কম নয়। এখানে সংক্ষেপে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা বাঞ্জনীয় বলে মনে হয় : সমগ্র পান্ডাত্ত-জগতে পুরনো বছরের অবসান ও নতুন বছরের আগমন সূচনার জন্য নর-নারী প্রমত্ত উল্লাসে ‘বল্-নাচ, মদ্যপান, কাঁসর-ঘণ্টা পিটানো, ও সিঙ্গা বাজানো, ভুরিভোজন, লোক-সঙ্গীত, প্রভৃতিতে মেতে উঠে। স্পেন শহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র প্রাক-নববর্ষ-সন্ধ্যায় (ড়হ ঘব িণবধৎ’ং ঊাব) লোকজন দলে দলে সমবেত হয়ে গান গেয়ে, নাচ নেচে, রকমারি ফুর্তি করে নতুন বছরের উৎসব পালনের জন্য প্রস’তি গ্রহণ করে এবং ‘নববর্ষের’ দিনে সকাল বেলায় ‘ম্যাস’ (গধংং) বা গির্জায় প্রার্থনা সেরে বন্ধু-বান্ধবদের সাক্ষাৎকারে, উপহার বিনিময়ে, ভোজনোৎসবে, অভিনন্দনে, আমোদ-প্রমোদে মেতে যায়। চীনারা নতুন বছরের প্রথম ক’দিন একটা সার্বজনীন উৎসবরূপে পালন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এখন তাঁরা তার জায়গায় ‘মে-ডে’ পালন করেন। উত্তর-ভারতের ‘নববর্ষের’ উৎসব ‘হোলি’ (সৎ-হোলাকা) বা ‘দোল’ সম্বন্ধে সকলেই অল্পবিস্তর অবগত। এটি বসন্তকালীন উৎসব। এতে ‘ফাল্গু’-খেলার ও পিচকারি মেরে রঙ ছিটিয়ে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করার রীতি এখনও বর্তমান আছে। দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়দের (বলা বাহুল্য- এই ‘দ্রাবিড়’দের রক্ত বাঙালীর মধ্যে পর্যাপ্ত) ‘নববর্ষ’ একটু ভিন্নরূপে পালিত হয়। তাঁরা তিন দিন ধরে এ উৎসব পালন করেন; তখন সর্বত্র একটা আনন্দমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। তাঁরা প্রথম দিনে নতুন চালে ‘নবান্ন’ পাক করে খাওয়াকে ‘নববর্ষের’ জন্য একটা সৌভাগ্যসূচক কাজ বলে মনে করেন। অধিকন’, এ সময়ে গবাদি পশুর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁরা এ-গুলোকে এদিকে ওদিকে তাড়িয়ে বেড়ান ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে উপহার বিনিময় করেন। এদের ‘নববর্ষ’ যে মূলে কৃষিভিত্তিক উৎসব, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
পৃথিবীর ‘নববর্ষের’ প্রাচীনতম উৎসবগুলোর মধ্যে ইরানীদের ‘নওরোজ’ অন্যতম। এ-টি ছ’দিনের উৎসব। ইরানীরা ‘নববর্ষের’ প্রথম দিনকে ‘নওরোজ-ই-কচুক’ (= ছোট নববর্ষ) এবং ষষ্ঠ দিনকে ‘নওরোজ-ই-বুজর্গ’ (= সম্ভ্রান্ত নববর্ষ) বলে উল্লেখ করে থাকেন। এক মহানন্দময় পরিবেশে পানাহার, নাচ, গান, বাদ্য ও উল্লাসের মধ্য দিয়ে ছয়দিন আগে নতুন দিনের (নওরোজের) যে উৎসব শুরু হয় ‘নওরোজ-ই-বুজর্গ’-এ তা চরমে উঠে শেষ হয়।
ইরানীদের এই যে ‘নওরোজ’, এর একটা মুসলিম-সম্পৃক্ত ইতিহাস আছে। মদিনা, উত্তর-ভারত ও পরিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের সাথেই এ ইতিহাসের যোগ দেখা যায়। হজরত মুহম্মদের (দঃ) আবির্ভাবের বছর চল্লিশেক আগে ‘য়থরিব’ বা মদিনা যখন পারস্য সাম্রাজ্যের পদানত ছিল, তথন ইরানীরা মদিনায় তাঁদের নিজস্ব ‘নওরোজ’ চালু করেন। হজরত যখন মদীনায় হিজরত করেন, তার দুই বছর পরে মুসলমানদের জন্য ‘ঈদ’ উৎসব প্রবর্তন করে তিনি মদীনা থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম জগত থেকে, ‘নওরোজ’ উৎসবকে বিতাড়িত করেন। তবে, মুসলিম ইরানে উৎসব হিসাবে ‘নওরোজ’ ও ‘ঈদ’ দুইটিই প্রতিপালিত হলেও, ‘নওরোজের’ জাঁকজমক, দীর্ঘতা, আনন্দ ও ভোগবিলাস প্রভৃতির দিক থেকে গুরুত্ব ‘ঈদ’ থেকে অনেক গুণে বেশী।
ইরান থেকে সম্রাট হুমায়ুন উৎসবটি (নওরোজ) উত্তর ভারতে আমদানী করেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বের (১৫৫৬-১৬০৫) গোড়া থেকেই ‘নওরোজ’ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। তাতে হেরেমবাসিনী নারীরা শখের দোকান সাজিয়ে ‘মীনা বাজার’ বা আনন্দ মেলাও বসাতেন। এমন এক ‘মীনা-বাজারে’ যুবরাজ সলীম (পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর) কুমারী মেহেরুন্নেসার (পরে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের) প্রেমে আত্মহারা হয়েছিলেন।
পাকিস্তান লাভের (১৯৪৭, ১৪ই আগস্ট) পর, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই নামসহ ‘নওরোজ’ পূর্ববঙ্গে (তখনও ‘পূর্ব-পাকিস্তান’ হয় নাই) চালু করা হয়নি বটে, তবে তার আনুষঙ্গিক ‘মীনা-বাজার’ অনুষ্ঠান চালু করার জোর প্রচেষ্টা ঢাকায় কয়েক বছর থেকেই চলে। এ-প্রচেষ্টা সক্রিয় সরকারী সহানুভূতিপুষ্ট ছিল কিনা, বলা যায় না। তবে বড় বড় সরকারী হোমরা চোমরাগণ ‘মীনা-বাজার’ বসানোর চেষ্টায় লিপ্ত থাকার খবর আমাদের অজানা নয়। ঢাকায় বসন্তকালে (‘নওরোজের’ সমকালে) বছর তিনেক মীনা-বাজার বসেছিল। কি কারণে জানি না, এই চেষ্টা বেশিদূর এগোয়নি।
এখানে এ-কথাও বলে দেওয়া আশ্যক যে, ‘বাংলা নববর্ষের’ কতখানি মিল বা গড়মিল আছে, তা সহজে খতিয়ে দেখার জন্যই উক্ত আলোচনার অবতারণা করা হেেয়ছে। তবে, ও-আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে সমস্ত বিষয় সকলের কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে নাও উঠতে পারে। এটা সত্য যে, আলোচনাটি একটা মোটামুটি ধারণা দিতে সমর্থ।
চার
যতই রকমারি ও ভিন্ন প্রকৃতির হোক, ‘নববর্ষের’ উৎসব এ অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা অতি সাধারণ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীব্যাপী নরনারী ‘নববর্ষে’ অনুভব করে যে, জীবন-ধারণের একটা কালচক্র (পুপষব ড়ভ ষরভব) সম্পূর্ণ আবর্তিত এবং আর একটা কালচক্র সবে আবর্তনোদ্যত। এ দুই আবর্তনের সন্ধিস’লে দাঁড়িয়ে তারা সবাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ‘নববর্ষের’ উৎসবে যোগ দিয়ে থাকে। তাদের এ উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোতে আশা, নিরাশা, আনন্দ, উল্লাস অথবা ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। তাদের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যাদি মিলে একটা জট পাকিয়ে ‘নববর্ষের’ উৎসবগুলোকে জটিল করে রেখেছে। এতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা বিভ্রান্ত হই। এতৎসত্ত্বেও, দুই একটি বিষয় অর্থাৎ অনুষ্ঠান এমন থাকে যে, সেগুলি গোপনে মূল বিষয়টির ইঙ্গিত দান করে। কিভাবে তা সম্ভব, তার প্রতি নীচে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।
ঘটা করে অনুষ্ঠান ‘নববর্ষ’ পালনের প্রাচীন ও আধুনিক রীতিনীতির প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায়, গোড়ার ‘নববর্ষ’ ছিল মানুষের ‘আর্তব-উৎসব’ বা ঋতুধর্মী উৎসব। ঋতুধর্মী বলে কৃষির সাথেও এর সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ, কৃষিকার্য একটি ঋতুনির্ভর মানব-বিজ্ঞান। তখনও মানুষের ধর্মাধর্মের বালাই ছিল না; চুলচেরা জ্যোতিষিক জ্ঞানও তার অর্জিত হয়নি। সে তখন চাঁদের ‘তিথি’ দেখে দিন, পক্ষ, মাস ও বছর গণনা করত- সে কথা পূর্বেই বলেছি।
তখনও মানুষ প্রকৃতির সন্তান। সভ্যতার কৃত্রিমতা তার সরল-সহজ জীবনকে জটিল করে তোলেনি। প্রাকৃতিক রীতিতে অর্থাৎ প্রকৃতির খেয়াল খুশির উপর নির্ভর করে তখনও তার জীবনধারা পরিচালিত হচ্ছিল। কৃষিই তার জীবনধারণের একমাত্র না হলেও প্রধানতম অবলম্বন। সে লক্ষ্য করত,- গ্রীষ্ম কালবৈশাখী সঙ্গে নিয়ে আসে, বর্ষা অঝোর ধারায় নামে, শরৎ মেঘ ও রৌদ্র খেলায় মাতে, হেমন্ত মাঠে সোনার ফসল ফলায়, শীত সে ফসল কুড়িয়ে ঘরে তোলার সুযোগ দেয় এবং বসন্ত ফুরফুরে হাওয়ায় মনকে মাতাল করে। এর সবই জড় ও জীব জগতে পরিবর্তন ঘটায়-নদ-নদী, পশু-পক্ষী, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত নতুন চেহারা ধারণ করে। মানুষ নিজেও তার মানস-লোকে এবং সর্বাঙ্গে এ-প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রভাব অনুভব করে।
কোন অনুভূতিকেই চেপে রাখা যায় না। ফুটন্ত জলের বাষ্পের মত সে প্রবলবেগে সকল বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে। এ-পথ যেমন নানান রকমের হয়, চাপা অনুভূতি প্রকাশের পথও হয় তেমন রকমারি। তাই, আদিম মানুষ গ্রীষ্মে জলের জন্য মেঘকে ডেকে বেড়াত, বর্ষায় শস্য বপনের সময় গান গেয়ে শ্রম বিনোদন করত, শরতে নৌকায়, ‘বাইচ’ খেলে অবকাশকে কর্মমুখর করে তুলত, হেমন্তে মাঠে মাঠে ‘টঙ’ বেঁধে আলো জ্বেলে শস্য পাহারা দিত, শীতে শস্য সংগ্রহের সময় দল বেঁধে রাত জাগত, গান (যেমন- জাগগান) গাইত ও আনন্দে নাচত এবং বসন্ত সমাগমে নাচ, গান, পান ও আহারে মেতে উঠত। এখনও আমাদের সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, জুমিয়া, চাকমা প্রভৃতি আদিম অধিবাসীরা এক এক ঋতুতে এক একভাবে তাদের মানসিক অনুভূতি প্রকাশ করলেও তার সাথে উক্ত ধারণার বহু বিষয়ে মিল আছে। সুতরাং, উক্ত রীতি কাল্পনিক হলেও, মূলতঃ সত্য। এ-গুলো আদিম মানুষের আর্তব অনুভূতিপ্রকাশক রীতি এবং এ-গুলোর সাথে কৃষির সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ। মনে রাখতে হবে, আজিকার সভ্য মানুষে যেমন আদিম মানুষ লুকিয়ে আছে, আজিকার মানুষের বহু সুমার্জিত রীতি-নীতিতেও প্রত্নমানবের বহু রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান অশ্মীভূত (ভড়ংংরষরুবফ) অবস’ায় লুকিয়ে আছে। এগুলোকে খুঁজে আবিষ্কার করার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা পৃথিবীর সর্বত্র এগিয়ে চলেছে।
এরপর, ধীরে ধীরে আদিম মানব-সভ্যতার বিবর্তন শুরু হল। চন্দ্র-সূর্য, নদ-নদী, পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত, অগ্নি-জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস’র মধ্যে মানুষ এক একটা অদৃশ্য-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করলে। ভূত-প্রেতে তার বিশ্বাস জন্মাল, আর সে তার কাছে মাথা নোয়ালে। এবার প্রাকৃতিক বস্তুপূজা শুরু হল,- চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, মেষ, সাপ, বেঙ, গাছ, পাথর কত কি, আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা পেতে লাগল। এবার পূজার জন্য আবশ্যক হল,- চন্দ্রসূর্যের উদয়াস্ত নির্ণয়, নানা ঋতুর স’ায়িত্বকালের অবধারণ এবং দিন, ক্ষণ, পক্ষ, মাস ও বৎসর গণনার জ্যোতিষিক জ্ঞান। সুতরাং, ‘নববর্ষ’ পালন শুরু হল বিশেষ ঋতুর পরিবর্তন দেখে। আগেকার ঋতু পরিবর্তনকালীন স্বতঃস্ফুর্ত নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ ও পানাহার জোরে সোরেই চালু রইল বটে, তবে তার সাথে যে নতুন উপসর্গ যুক্ত হল, তাকে বলা যায় বিশ্বাস অনুশাসিত অনুষ্ঠানপূর্ণ উৎসব।
মানুষ যেদিন অদৃশ্য-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছিল, সে-দিনই তার মনে তার একান্ত অলক্ষ্যে ধর্মের বীজ উপ্ত হয়। তেত্রিশ কোটি অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বের অনুভূতি ও বিশ্বাস থেকে তিনটিতে নেমে আসতে মানুষের কত কাল লেগেছিল, বলা যায় না। তবে, ‘তিন’ থেকে ‘একে’ এসে পৌঁছুতে তার মাত্র ছয় শত বছর লেগেছিল। এই যুগ হচ্ছে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের যুগ। এর প্রভাব পৃথিবীর ‘নববর্ষের’ উৎসবে সর্বাধিক।
যুগে যুগে এভাবে মানুষের ধারণা ও বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ তার পশু-প্রকৃতিকে (ধহরসধষরঃু) বুদ্ধিবৃত্তি (ৎধঃরড়হধষরঃু) দিয়ে জয় করতে পারুক বা না পারুক, অন্ততঃ পক্ষে তাকে বহুগুণে মহত্তর (ংঁনষরসব) করে তুলেছে। অধুনা, বিশ্বময় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির জয় বিঘোষিত হলেও, তার পশুপ্রবৃত্তির বিলয় ঘটেনি। যদি তা হত, তা হলে আজও পৃথিবীময় চুরি-ডাকাতি, নরহত্যা, লুটতরাজ এমন কি, যুদ্ধবিগ্রহও সংঘটিত হত না। এই একই ব্যাপার আজিকার সভ্য মানুষের ধর্মানুশাসিত আচার-বিচার, রীতি-নীতি, বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যেই হরহামেশা দেখতে পাই। তাই, আজও আমরা প্রাচীনতম ঐতিহ্যের ধারাবাহী পীর-ফকীরে বিশ্বাস করি, কবচ তাবিজে আস’া রাখি এবং ভূত-প্রেতে ভয় পাই। কেননা, প্রাকৃতিক বস’র দৃশ্য-শক্তিতে বিশ্বাসী আদিম মানুষেরা দীর্ঘায়ু ছিল না বলে মনে করত, মানুষ বৃদ্ধ হলেই অদৃশ্য-শক্তির অধিকারী হয় এবং মরলে ভূত হয়ে বেঁচে থাকে। ‘মরে ভূত হওয়া’ বাংলা বাগ-গুচ্ছটিও (ঢ়যৎধংব) এখানে স্মর্তব্য। ‘বৃদ্ধ’ অর্থে সংস্কৃত ‘স’বির’, পালি ‘থের’ (বৌদ্ধদের ‘থেরবাদ’), ফারসী ‘পীর’ শব্দগুলিও এই প্রসঙ্গে তুলনামূলকভাবে মনে করা যেতে পারে।
আজও পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে; আজও পৃথিবী বিভিন্ন ঋতুতে তার রূপ পালটায়; আজও মানুষের দেহমনে তার ছোঁয়া লাগে; আজও মানুষ ভিন্ন-ভিন্ন সময় বিশ্বময় ‘নববর্ষ’ উদযাপন করে। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি নিয়ে ‘নববর্ষের’ অনুষ্ঠানাদির বিচার করলে দেখা যায়, আজিকার নর-নারীর মধ্যে যেভাবে আদম হাওয়া বেঁচে আছেন, আজিকার ‘নববর্ষের’ অনুষ্ঠানাদির মধ্যেও তেমনভাবে আদিম যুগের ঋতুধর্মী (আর্তব) নাচ, গান, বাদ্য, পানাহার সমন্বিত আনন্দমুখর উৎসবের পরিবেশ ভব্যবেশে আত্মগোপন করে রয়েছে। কেননা, বর্তমান হচ্ছে অতীতের ভোল-পালটানো রূপ একথা অস্বীকার করলে আত্মপ্রবঞ্চনাই করা হবে।
পাঁচ
এবার আমাদের দেশে ‘নববর্ষের’ উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা করা যেতে পারে। এ-ব্যাপারে আমাদের ‘নববর্ষের’ সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ‘নববর্ষের’ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল নেই;- থাকতেও পারে না। কারণ, সব দেশের ভৌগোলিক অবস’ান, আবহাওয়া ও মানব-গোষ্ঠী এক নয়। আমাদের ‘নববর্ষ’ আমাদের ভৌগোলিক অবস’ান, আবহাওয়া ও মানব-গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবিত; আর অন্যান্য দেশের ‘নববর্ষ’ স্বীয়-স্বীয় ভৌগোলিক অবস’ান, আবহাওয়া ও মানব-গোষ্ঠীর প্রভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
বর্তমানে ‘বাংলা নববর্ষ’ ও ‘পয়লা বৈশাখ’ সমার্থক বাগ গুচ্ছ (ঢ়যৎধংব)। এই দুই বাগ্-গুচ্ছ সমার্থকতা লাভ করতে সহস্র সহস্র বৎসর আবশ্যক হয়েছিল। তার কারণ এই : ‘নববর্ষ’ আদিম মানব-গোষ্ঠীর ‘আর্তব উৎসব’ (ংবধংড়হধষ ভবংঃরাধষ) এবং ‘নববর্ষ’ হিসাবে ‘পয়লা বৈশাখ’ সভ্য মানুষের ‘কৃষুৎসব’ (ধমৎরপঁষঃঁৎধষ ভবংঃরাধষ)। আদিম যুগে মানুষ যখন যাযাবর জীবন-যাপন করত তখন সে স্বাভাবিক নিয়মেই ঋতু পরিবর্তনের সময় কালোপযোগী উৎসব পালন করত। সে যখন কৃষি-বিজ্ঞান আবিষ্কার করে স’ায়িভাবে এক জায়গায় বসবাস করতে শিখল তখন সে হল গৃহী। উপর্যুক্ত ঋতু দেখেই গৃহীকে শস্য বুনতে ও ঘরে তুলতে হয়। তখন সে চাঁদ দেখে বার চাঁদে বছর গুনতে শিখেছে; কেননা শস্য বোনার এক ঋতু থেকে আর এক ঋতুতে আসতে তার লেগে যেত বার চাঁদ। প্রতিমাসে একবার করে পূর্ণিমা হয়, আর পূর্ণিমায় চাঁদ রাশিচক্রের যে-নক্ষত্র (যেমন বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, আষাঢ়া, শ্রাবণা প্রভৃতি) দাঁড়িয়ে পূর্ণরূপে দেখায়, সে নক্ষত্রের নামানুসারে সে চান্দ্রমাসের নাম দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ্য প্রভৃতি চান্দ্রমাসের নাম; যদিও জটিল জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনার সাহায্যে সৌর বৎসরের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে (অর্থাৎ চান্দ্র বৎসরকে প্রায় সাড়ে দশ দিন বাড়িয়ে দিয়ে) চান্দ্রমাসগুলোকে স্বীয়-স্বীয় নামে সৌরমাস হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। এখনও তাই হচ্ছে। সুতরাং গ্রীষ্মঋতুসূচক ‘পয়লা বৈশাখ’ পূর্ববর্তী ‘আর্তব নববর্ষের’ সাথে এক হয়ে যেতে বহু শতাব্দী আবশ্যক হয়েছে। আমাদের দেশের মানব-সভ্যতা তখন অনেক দূর এগিয়ে জ্যোতিষ যুগে প্রবেশ করেছে।
এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই,- পৃথিবীর কোন অঞ্চলে ‘নববর্ষের’ উৎসব অনুষ্ঠিত হত শীতকালে, কোন অঞ্চলে বসন্তকালে, আর কোন অঞ্চলে শরৎকালে। যেখানে যে ঋতু প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে সে ঋতুকেই কেন্দ্র করে প্রধান উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। তদুপরি ছোটখাট ‘আর্তব উৎসব’ যে গ্রীষ্মকালে ছিল তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর সর্বত্র গ্রীষ্মকালীন প্রধান উৎসবও ‘নববর্ষের’ উৎসব রূপে পরিগণিত হয়েছে, আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালীন প্রধান উৎসবও ‘নববর্ষের’ উৎসব রূপে পরিগণিত হয়ে থাকবে। আমার মনে হয়, ‘কালবৈশাখীর তাণ্ডব-লীলা ও তার পরে পরেই প্রকৃতির নতুন সৃষ্টির যে রূপটি বাংলা দেশে দেখা দিয়ে থাকে, তাই আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে গ্রীষ্মকালের এবং গ্রীষ্মকালীন উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছিল। নইলে এখানকার ‘নববর্ষের’ অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি ধর্মের প্রভাবে বিপুলভাবে প্রভাবিত হত। কেননা আমাদের দেশ আদিম অধিবাসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীস্টান অধ্যুষিত দেশ। অথচ, এ সমস্ত ধর্মের কোন বিশিষ্ট প্রভাব আমাদের ‘নববর্ষের’ অনুষ্ঠানে ও উৎসবে দেখা যায় না।
এখানে কেউ কেউ ‘বাংলা নববর্ষের’ একটা প্রধান অনুষ্ঠান ‘হালখাতায়’ ধর্মের প্রভাবের কথা উল্লেখ করতে পারেন। দেখা যায়, ‘হালখাতার’ মাথায় প্রায়ই একটা-না-একটা স্বস্তিবাচন লিখিত থাকে। কোন মুসলমান ব্যবসায়ী যদি তাঁর ‘হালখাতার’ মাথায় ‘এলাহী ভরসা’; হিন্দু ব্যবসায়ী ‘নমো গণেমায় নমঃ’; বৌদ্ধ ব্যবসায়ী ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরনং গচ্ছামি, সঙঘং শরণং গচ্ছামি’ এবং কোন খ্রীস্টান ব্যবসায়ী একটা ‘ক্রুশ’ এঁকে নিয়ে বা লিখে দিয়ে তাঁদের ‘হালখাতা’ খুলে থাকেন, তাতে ‘বাংলা নববর্ষের’ এ অনুষ্ঠানকে ধর্ম প্রভাবিত বলা চলে না। কারণ, এটা ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি মাত্র; হালখাতায় লিখিতব্য হিসাব-নিকাশের অঙ্গ নয়। এটা লিখলেও যেমন ‘হালখাতা’ হিসাবের বই-ই থাকে, না লিখলেও তেমন ‘হালখাতার’ হালখাতাত্ব যায় না। এতে ‘হালখাতা’ খোলার উদ্দেশ্য ও রীতি-নীতের কোন পরিবর্তন ঘটে না; তার প্রয়োজনীয়তারও কোন তারতম্য দেখা দেয় না। সুতরাং ‘হালখাতার’ মালিকের আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে এবং বিশ্বাস হচ্ছে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।
বর্তমানে ‘হালখাতা’ ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান হলেও, আসলে এ হচ্ছে একটা কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান। প্রাচীন কালে ‘দ্রব্য’-বিনিময়ের মাধ্যমে (‘মুদ্রা’ বিনিময়ের মাধ্যমে নয়) যখন ব্যবসা চলত তখন গৃহস্বামী তার উৎপন্ন দ্রব্যের কতটুকু নিজের জন্য রেখে, অবশিষ্টটুকুর দ্বারা তার প্রয়োজনীয় অন্য দ্রব্য নেবে, সে সম্বন্ধে একটা হিসাব যে কোন উপায়ে, যেমন রশিতে গেরো দিয়ে, পাথরের বা মাটির ঢেলার স্তূপ জমিয়ে, তাকে রাখতে হত। তারপরে অনেক অনেক পরে, সে তালের পাতায় ‘টোকা’ রেখে অথবা তুলট কাগজে ‘চোতা’ বানিয়ে ঐ কাজ সেরেছে। বর্তমান ‘হালখাতা’ তারই বিবর্তিত রূপ।
‘পুণ্যাহ’ অনুষ্ঠান এখন আর নেই। যখন ছিল, তখনও এতে কোন ধর্মীয় অনুশাসন অথবা ক্রিয়াকলাপ ছিল না। এ ছিল জমিদার প্রজার মধ্যে মিলন ঘটানো ও সদিচ্ছা বিনিময় করার মাধ্যমে খাজনা আদায়ের প্রীতিপূর্ণ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানও ছিল একান্ত কৃষিভিত্তিক। কারণ, জমিতে ফলন না হলে প্রজারা কি করে খাজনা দেবে? বলা বাহুল্য, এ খাজনা দেওয়ার রীতিটিও ছিল প্রথমে উৎপন্ন ফসলের দ্বারা এবং পরে মুদ্রার মাধ্যমে। এখানে সংস্কৃত ‘বহুব্রীহি’ {বহু (অনেক) ব্রীহি (ধান্য) আছে যাহার সেই ব্যক্তি} ‘ধানের জমিদার’ অর্থে ব্যবহৃত শব্দটিও স্মরণ করা যেতে পারে।
‘পুণ্যাহ’-এর মতো আরও একটি অধুনা লুপ্ত কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। ‘পয়লা বৈশাখে’ বা ‘বাংলা-নববর্ষে’ ঢাকার মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে যে ‘গরুর দৌড়’ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত, তা এখন লোপ পেলেও, এতে ধর্মীয় সংস্রব ছিল না। এ অনুষ্ঠানের মতো একটি ‘নববর্ষের’ অনুষ্ঠান দক্ষিণ ভারতে এখনও প্রচলিত আছে। তাঁরা ‘নববর্ষে’ গবাদি পশুকে পুষ্পসজ্জিত করে এদিক সেদিক ঘুরায়ে বেড়ায়। দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় জাতের এ রীতি আমাদের মধ্যে থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ, বাঙালীদের মধ্যে দ্রাবিড় রক্তের অসদ্ভাব নেই।
‘মেলা’ পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অতি প্রাচীন, অথচ সাধারণ অনুষ্ঠান। আমরা নানা সূত্রে গ্রীস-দেশের থেসালীতে অনুষ্ঠিত ‘অলিম্পিক মেলার’ এবং আরব দেশের মক্কায় অনুষ্ঠিত ‘উকাজ’-এর মেলার বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারি। ‘অলিম্পিক’ মেলার’ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ‘উকাজের’ মেলার দ্যূতক্রীড়া, ঘোড়দৌড় ও সাহিত্য প্রতিযোগিতা প্রসিদ্ধ ছিল। এ সমস্ত মেলায় পণ্যদ্রব্যের বিকিকিনিও হত। আমাদের দেশের ‘নববর্ষের’ মেলাগুলোও এদেশের প্রাচীনতম ‘আর্তব উৎসব’ ও ‘কৃষ্যুৎসব’ প্রভৃতির বিবর্তিত রূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা, এ-গুলোতে এখন পর্যন্ত স’ানীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির বেচা কেনা হয়। এখানে মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর অধিকাংশ মেলায় ধীরে ধীরে ধর্মের নানা প্রভাব ঢুকলেও, আজও তেমন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমাদের এ-মেলাগুলোতে ঢোকেনি।
‘বলীখেলা’ গ্রীক দেশের ‘অলিম্পিক-ক্রীড়া’ জাতীয় ব্যাপার হলেও আমাদের দেশের ‘বলীখেলায়’ অলিম্পিকের কোন প্রভাব নেই। কারণ, ‘অলিম্পিক’ ধর্মসম্পৃক্ত ক্রীড়া; তার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান হচ্ছে অগ্নি-পূজায়। আজও অলিম্পিক-ক্রীড়ায় মশালের আগুন জ্বেলে ক্রীড়ার উদ্বোধন করা হয়। অথচ, ‘বলীখেলায়’ তেমন কোন অনুষ্ঠান দেখা যায় না। আমাদের দেশে ছিল ‘মল্লক্রীড়া’ এবং এর প্রদর্শন ক্ষেত্র ছিল মল্লভূমি। এই ‘মল্লক্রীড়ায়’ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের যোগ ছিল না। আমাদের দেশের বলীখেলা প্রাচীন ‘মল্লক্রীড়ার’ উত্তর-পুরুষ। এতে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই।
ভারতের মালদহ ও পাকিস্তানের রাজশাহীর ‘গম্ভীরা’ অনুষ্ঠানটি ‘বাংলা নববর্ষের’ একটা বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। ইহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে (এখন থেকে প্রায় ১০১ বছর আগে -সম্পাদক) পন্ডিত হরিদাস পালিত তাঁর ‘আদ্যের গম্ভীরা’ নামক গ্রনে’ (প্রায় ৬০ বৎসর আগে প্রকাশিত) বলেছেন যে ‘গম্ভীরা’ শিবের ‘গাজনের’ বিবর্তিত রূপ। কেননা, এ গানগুলোতে ‘ভোলা’-কে (ভালানাথকে=শিবকে) সম্বোধন করে গায়েনরা সমাজের সুখ-দুঃখের চিত্র সকলের কাছে তুলে ধরেন। তিনি (হরিদাশ বাবু) বোধ হয় লক্ষ্য করেননি যে, ‘শিবের গাজন’ হয় চৈত্রসংক্রান্তির দিনে,- বৈশাখ মাসে নয়। সারা বৈশাখ মাস ধরে ‘গম্ভীরা’ অনুষ্ঠিত হয় কেন, সে বিষয়েও তিনি খোলাখুলিভাবে কিছু বলেন নি।
মুসলমানেরা মনে করেন, ‘ভোলা’ শিব বা ‘ভোলানাথ’ নয়। তাঁদের মতে যে লোক সবকিছু ভুলে গিয়ে কর্তব্য কর্মে অবহেলা করে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছে, সেই ব্যক্তিই ‘ভোলা’। তাঁরা আরও বলেন, ‘গম্ভীরা’ হচ্ছে আগত সালে বিগত বছরের দুঃখ-দুর্দশার পুনরুক্তি বন্ধের জন্য কঠোর সমালোচনামূলক ‘সালতামামীর গান’। এর নাচের অংশ ‘আর্তব উৎসবে’র অংশবিশেষরূপে পরিগণিত লোকনৃত্যের বিবর্তিত রূপ। ‘গম্ভীরা’ মূলে শিবের গাজন হলেও হতে পারে। এখন তা বিবর্তিত হয়ে যে রূপ ধারণ করেছে তাতে ‘শিব’ মরে ‘মামদো’-ভূতে পরিণত হয়েছে।
‘বাংলা নববর্ষ’ এ দেশের একটা প্রাচীনতম ঐতিহ্য। পয়লা বৈশাখের উৎসবের মধ্য দিয়ে এ-দেশের নরনারী এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সঙ্গীত, নৃত্য, আমোদ-প্রমোদ, পানাহার প্রভৃতি পৃথিবীর যে কোন প্রাচীন ও নবীন উৎসবের একটা অতি সাধারণ অঙ্গ। প্রাচীনকালের ‘আর্তব উৎসব’ থেকে আধুনিক যুগে এসে এ-গুলো ভোল পালটিয়েছে বটে’, তবে তাদের মৌলিক সত্তা কখনও হারায়নি। তার প্রমাণ পাচ্ছি বাংলা প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের কাব্যে, গানে, গাথায় ও বারমাসীতে। এগুলোতে বৈশাখে ‘নববর্ষের’ আগমনে আমাদের দেশের মানুষের চিত্তে যে চেতনার পরিচয় পাই, তাতে ঋতু পরিবর্তনের অমোঘ প্রভাব সূচিত হয়। তাই বলতে হয়, ‘বাংলা নববর্ষ’ আর্তব উৎসব এবং কৃষ্যুৎসবও বটে। এর সাথে ধর্মের কোন সংস্রব নেই বললেই চলে।
আমাদের অধুনাতন ‘নববর্ষ’ এ-দেশের গ্রীষ্মকালীন ‘আর্তব উৎসব’ ও কৃষ্যুৎসব’ উদযাপনের একটা বিবর্তিত নবসংস্করণ। এর ঐতিহ্য প্রাচীন, কিন’ রূপ নতুন। নতুন সংস্কার, নতুন সংস্কৃতি, নতুন চিন্তাধারা অবারিত স্রোতে যুক্ত হয়ে এতে সৃষ্টি করেছে এমন এক নতুন আবহ, যাকে একটা দার্শনিক পরিমণ্ডল বলে উল্লেখ করতে হয়। এ পরিমণ্ডলে পুরাতন বিলীন, জরাসতূপ নিন্ডিহ্ন, মিথ্যা বিলুপ্ত ও অসত্য অদৃশ্য। আর নতুন আবির্ভূত, নবজীবন জাগরিত, সুন্দর সুস্মিত ও মঙ্গল সম্ভাবিত। ‘কাল-বৈশাখীই’ এর প্রতীক। সে ‘নববর্ষের’ অমোঘ সহচর, নব-সৃষ্টির অগ্রদূত, সুন্দরের অগ্রপথিক ও নতুনের বিজয়-কেতন। তাই, আজিকার দিনে কবি কালবৈশাখী দেখে গেয়ে উঠেন,-
‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর,-
ওই নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর’।
[নিবন্ধটি মোবারক হোসেন সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী থেকে পহেলা বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ’ সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে লেখকের বানান-রীতি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।